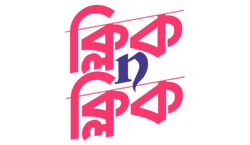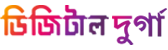শিউলি ছড়িয়ে ছোট্ট চাতাল জুড়ে
রোদ ওঠে যেন বিসমিল্লার সুরে।
আকাশের কোন ঠিকানায় চিঠি আসে?
শরৎ কি খুব সাদা ফুল ভালবাসে?
ফুল পড়ে থাকা পথ ধরে চলে যাওয়া,
পৌঁছেও দেখে বাকি কতকিছু চাওয়া।
উঠোনে অতিথি ক্ষণিকের আলপনা,
তারায় তারায়; মেঘে মেঘে আনাগোনা।
যে তারা প্রয়াত, সেও আলো নিয়ে আসে,
শরৎ কি খুব সাদা ফুল ভালবাসে?

কারণ সামান্য। সামান্য কারণেই সকাল থেকে মনটা তেতো হয়ে আছে সুব্রতর। এতটাই তিতকুটে যে এই সিগারেট-বিলাসিতার সময়েও জিভটা খরখরে লাগছে। তেতো মনের বিস্বাদ যেন জমা হচ্ছে সিগারেটের ফিল্টারে। বিরক্ত লাগে সুব্রতর, বুক ভরে বিলাসিতার ধোঁয়া নেওয়াটা উপভোগ করতে না পারার জন্য।
প্রত্যেকদিন এই ফুরিয়ে আসা দুপুরে রুটি-আলুভাজার ঢেঁকুর তুলতে তুলতে সিগারেট খাওয়াটা সুব্রতর কাছে বিলাসিতা মনে হয়। বিলাসিতা মনে হয় যেহেতু ওর মতো গরিব মানুষদের সিগারেট খেতে নেই বা এমনটাও হতে পারে ফুটপাতের ঘড়ির দোকানের সার্ভিসম্যান কাম সেলসম্যান কাম ক্যাশিয়ার কাম কমনম্যানদের সিগারেট খেতে নেই। আর তাই ঘরের বউকে লুকিয়ে পর্নোগ্রাফি দেখার মতো দোকান মালিককে লুকিয়ে সারাদিনের এই একটামাত্র সিগারেট-সুখ ওর ঠোঁটে পুড়তে থাকে। ধরে নেওয়া যেতে পারে এই সময়টা ও নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। কোনও কোনও দিন এই নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডের বোধ ওর বিলাসিতার মাত্রাকে বাড়িয়ে দেয়। সেইসব দিনগুলোতে তিন হাজারি মাস-মাইনের সুব্রত আগুনজ্বলা রোদে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখে। এই ঘড়িপাড়ায় ওর একটা নিজস্ব শো-রুম হয়েছে। কলকাতার একমাত্র শো-রুম যেখানে শুধু রোলেক্স বিক্রি হয়। শিপ্রাকে নিয়ে পুরী বা দার্জিলিং বেড়াতে গেছে। ওর আর শিপ্রার কারোরই সমুদ্র বা পাহাড় দেখা হয়নি। সমুদ্র বা পাহাড় কেন, বিয়ের নয় বছরে পাশের পাড়াটাও ঠিকঠাক দেখা হয়নি। যেমন শুভকেও একটা ঠিকঠাক স্কুলে ভর্তি করা যায়নি। শিপ্রার ইচ্ছে ছিল শুভকে কনভেন্টে দেওয়ার, কিন্তু সেকথা ভাবলেই সুব্রতর বুকটা ধক করে ওঠে। শো-রুমটা হয়ে গেলে শুভকে নামকরা স্কুলে দেবে এবং অবশ্যই একটা বাড়ি করবে।
এই বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে কোম্পানিতে আগুন লেগে যায় প্রতিবার। তর্জনী ও অনামিকার ফাঁকে গোঁজা সিগারেটের আগুন কোম্পানি পুড়িয়ে ফিলটারে লাগে। আঙুলে ছ্যাঁকা দেয়। ফিল্টারটা ছুঁড়ে ফেলে হেসে ওঠে সুব্রত। ধুস, কুঁজোর আবার চিত হয়ে শোওয়া। ফুটপাতের ঘড়ির দোকানের সার্ভিসম্যান কাম সেলসম্যান কাম ক্যাশিয়ার কাম কমনম্যানদের এরকমই হয়। এর মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু অস্বাভাবিকতা হল আজকে সুব্রতর দ্বিতীয় সিগারেট কেনাটা।
দুটো সিগারেট মানে তো একের বেশি। সুব্রত এর আগে একের বেশি সিগারেট কিনেছিল মাত্র দু’বার। নয় বছর আগে নিজের বউভাতের দিন বন্ধুদের আপ্যায়নের জন্য সর্বোচ্চ দেড় প্যাকেট এবং বছর ছয়েক আগে শুভ হওয়ার দিন আনন্দে নিজের জন্য দু’টো সিগারেট কিনেছিল সুব্রত। আসলে তেতো মনটাই ওকে অসংযমী করে তুলেছে। চুরির মতো একটা সাময়িক ভয় রক্তের সঙ্গে মিশে শিরায়-শিরায় বয়ে যাচ্ছে কাল রাত থেকে। সারা শরীরে ভয় বয়ে চলেছে, শুভ শেষ পর্যন্ত চোর হয়ে যাবে না তো!
ফুটপাতের ঘড়ির দোকানের সার্ভিসম্যান কাম সেলসম্যান কাম ক্যাশিয়ার কাম কমনম্যান তিন হাজারিদের এই একটা সমস্যা। অতি সাধারণ ঘটনাতেও ভয় পাওয়া। নিজে নিজেই ভয়ের বিস্তার ঘটানো। ভয়ের ডালপালা ছড়িয়ে-ছড়িয়ে বিষণ্ণ হয়ে পড়া। সিঁটিয়ে যাওয়া।
আর পাঁচটা বাচ্চার মতো লোভে পড়েছিল শুভ। লিচুর লোভ। গাছ পাকা নয়। রবারের। লাল টকটকে লিচু রবার। এখন ওইরকমটাই চল। হামেশাই পাওয়া যায়। লিচু আতা আম ঘোড়া হাতি গাড়ি রবার। সাদা চৌকো রবার বাচ্চারা এখন আর ছুঁতে চায় না। সবে লেখা ধরেছে শুভ। পেনসিলে। ওর রবারটা কিন্তু সাদা চৌকো। আদিমতা মেশানো একঘেয়ে। কাল রাতে স্কুলের ব্যাগ গোছাতে গিয়ে রবারটা চোখে পড়ে শিপ্রার। শুভ তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, হয়তো সেই জন্য ওর কাছে কিছু না জানতে চেয়েই একক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল শিপ্রা, শুভ লিচু চুরি করেছে। ওর প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল অনেকটা ইনস্যাস থেকে গুলি ছিটকে আসার মতো— “কী সর্বনাশ হল! ছেলেটা চোর হয়ে গেছে।”
সব দেখেশুনে সুব্রতও সিদ্ধান্ত নিয়েছে ছেলেটা চোরই হয়ে গেল। ওর এই সিদ্ধান্তে আসার সহায়ক হয়েছিল ওর পরিবেশ। মফস্বলে গজিয়ে ওঠা হঠাৎ-কলোনিতে দশ বছরের ছেলেরাও আড়ালে পোড়া-বিড়ি ফোঁকে, ফ্ল্যাটবাড়ির বন্ধ দরজার সামনে থেকে জুতো সরায়, পকেট ফসকে পড়ে যাওয়া মোবাইল কুড়িয়ে পর্ন দেখে। শিপ্রা আড়াল করতে চাইলেও বাঁচিয়ে রাখতে পারে না শুভকে। ওদের সঙ্গে মিশে যায়। মিশেই যায়। এই মিশতে মিশতেই শিখে যায় চুরি, টকটকে লাল লিচু চুরি। তাই রাতেই ফুটপাতের ঘড়ির দোকানের সার্ভিসম্যান কাম সেলসম্যান কাম ক্যাশিয়ার কাম কমনম্যান সুব্রত সিদ্ধান্ত নেয় হঠাৎ-কলোনিটা ছাড়তে হবে। উঠে যাবে কোনও ভদ্র পাড়ায়। এই পাড়াটা পাল্টাতে হবে। পাল্টাতেই হবে শুভকে মানুষ করার জন্য।
আজ সকালে কিন্তু শুভ বলেছে ও চুরি করেনি। শিপ্রা-সুব্রত দু’জনেই বোঝে ছেলেটা মিথ্যে বলছে। অভাবী স্কুলে হাভাতে বন্ধু— কেন দেবে এমন রবার। সুব্রত ছেলেকে বোঝায় আর ভয় পায়, ছেলেটা চুরির সঙ্গে মিথ্যে বলতেও শিখেছে!
দ্বিতীয় সিগারেটেও মজা পেল না সুব্রত। ভাঙা মেজাজ নিয়েই দোকানে ফিরে এল ও।
দুই
বাজারে এসে মনটা আরও তেতো হয়ে গেল সুব্রতর। একেবারে নিমফল। ফুটপাতের ঘড়ির দোকানের সার্ভিসম্যান কাম সেলসম্যান কাম ক্যাশিয়ার কাম কমনম্যান সুব্রত ফেরার ট্রেন ধরার আগে কোলে মার্কেট থেকে বাজারটা সেরে নেয়। কিছুটা সস্তা পড়ে। সস্তা পড়লেও কোনও কিছুই আর কিলোতে বিক্রি হয় না। হয়ত কিলোতে চড়া দামটা কানে বাজে। তাই এখন সবই বিক্রি হয় আড়াশো দরে। আড়াশোর দামটাও ইদানীং কানে বাজে। বিভ্রান্ত করে। প্রত্যেকদিনই। তবু ওকে কিনতে হয় পেটের খিদের, জিভের লোভের জন্য। এই পেট-জিভ যাপনের জন্যই বাজারের মধ্যে এসে দাঁড়ায় সুব্রত। সপ্তাহে তিনদিন। চল্লিশটাকা বরাদ্দে দু’দিনের বাজার। সপ্তাহে একদিন মাছ। রোববার। সেদিন এলাকার বাজারেই নির্ভর করতে হয়। অন্যান্যদিন ডাল আলুসেদ্ধ ভাজা তরকারি— শিপ্রা গুছিয়ে রান্না করে বেশ।
তরকারির কথায় মনে এল অনেকদিন পাঁচ-তরকারি খায়নি। আহা! শিপ্রা রাঁধে ভালো। ডুমো-ডুমো আলু বেগুন ঝিঙে কুমড়ো ডাঁটা দিয়ে মাখো-মাখো। কাঁচা লঙ্কা-পাঁচফোড়নের গন্ধ, হালকা সর্ষেবাটা। জিভে জল আসে ওর। ভাবতেই মনের তেতো ভাবটা কাটতে থাকে। আজ পাঁচ-তরকারির বাজার করবে সুব্রত। শিপ্রা একফালি লাউ নিতে বলেছে। রবিবার মাছ খাওয়ার দিন। একমুঠো কুচো চিংড়ি। সুব্রত বুঝতে পারে এই সপ্তাহের ছুটির দিনটা জমে যাবে।
কিন্তু সজনে-ডাঁটায় হাত দিতেই আঙুলের ডগাগুলো পুড়ে গেল। মাসি বলে কী! সজনে কিনলে তো বাজার-বরাদ্দটাই শেষ হয়ে যাবে। সজনে থেকে সরে বেগুনে চোখ রাখল। তেল-চকচকে বেগুন। সর্ষে দিয়ে ভর্তা। অথবা ভাজা। একটা কাঁচা লঙ্কা। জিভে জল এল ওর। শেষ কবে খেয়েছিল মনে করতে পারে না। কিন্তু এবার যেন গোটা হাতটাই পুড়ে গেল। ঝিঙে লাউ কুমড়ো লঙ্কা— বাজার ঘুরতে-ঘুরতে পুরো শরীরটাই পুড়ে গেল ওর। মাথায় আগুন চেপে বসল। নিয়ন্ত্রণহীন দামের জন্য কাকে দোষ দেবে খুঁজে না পেয়ে ফুটপাতের ঘড়ির দোকানের সার্ভিসম্যান কাম সেলসম্যান কাম ক্যাশিয়ার কাম কমনম্যান নিজেকেই দোষ দিল। ইচ্ছে হল নিজের গালে ঠাঁটিয়ে চড় মারতে। এই বাজারে কে বলেছিল তিন-হাজারিকে বিয়ে করতে! শুভর বাপ হতে! সংসারপালনে যোগ্যহীন মনে হল নিজেকে। ইচ্ছে হল নিজেকে বিদ্রুপ করতে, তিন-হাজারির আবার সংসার! বাজারের মাঝে দাঁড়িয়ে হিংসা হল ব্যাগ-ভর্তি মানুষগুলোকে দেখে। চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে, চা খাচ্ছে, আড্ডার মেজাজে মানুষগুলো কতো-হাজারি!
হিংসা হল কলোনির অনেককে। ওর থেকে কম-হাজারি হয়েও অনেকের ঠোঁটে দামি সিগারেট জ্বলে, রাতে মুখ থেকে বিলাতি মদের গন্ধ ছাড়ে। রংচঙে জামাকাপড় পরে। হাতে ঝলমল করে ক্যামেরা মোবাইল। নিজের ম্যাড়ম্যাড়ে জীবনটাকে ঘৃণা হল সুব্রতর। সংসারপালনে যোগ্যহীন সুব্রতর ইচ্ছে হল স্বার্থপর হওয়ার। এবং তখনই ঠিক করল বাজার-বরাদ্দের চল্লিশ আজ নিজের জন্যই ব্যয় করবে আজ। এখনই। ডুবে যাবে বিলাসিতায়।
রাস্তার পাশে একটা চায়ের দোকানে এসে দাঁড়াল সুব্রত। জমাটি দোকান। বাজার-ফেরতা অনেক-হাজারিরা তখন আড্ডায় ব্যস্ত। সুব্রত দোকানে দাঁড়িয়ে এক প্যাকেট সিগারেট কিনল। একটানে সিগারেটের প্যাকেটটা খুলে ফেলল। স্পেশাল চায়ের বরাত দিয়ে সিগারেট ধরাল। আড়চোখে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করল কেউ ওকে দেখছে কিনা। হতাশ হল। কেউ ওকে দেখছে না। সবাই আড্ডায় মশগুল। ইচ্ছে হল ওদের সঙ্গে আড্ডা মারতে। কতকাল আড্ডা মারা হয়নি। ওরা তখন বাজারদর ফোড়ে প্রশাসনের কথায় ওলট-পালট খাচ্ছে।
সুব্রত ওদের কথার কোনো ধরতাই পায় না। বিষয়গুলো নতুন মনে হয়। মিশতে পারে না। অথবা এমনটাও হতে পারে ওর পোশাক-চোখ-মুখ-শরীরের দীনতায় আড্ডাবাজরাই ওর সঙ্গে মিশতে পারছিল না। ওর আবার রাগ হল। ভাঁড়ে শেষ চুমুক দিয়ে আরও একটা সিগারেট ধরাল। আড্ডাবাজদের কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করল। চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগল ওদের হাত-মুখ, শরীরী ভঙ্গি। শুধু ঠোঁট নয়, আড্ডা-তর্কে ওদের শরীরও যেন কথা বলছে। আর ঠিক তখনই চোখ আটকে গেল ওর পাশে বসা আড্ডাবাজের পায়ের কাছে। বেঞ্চির গায়ে ব্যাগ ভর্তি বাজার পিসা’র হেলানো গির্জার মতো কাত করে রাখা। সজনে ডাঁটাগুলো অর্ধেক বেরিয়ে আছে। তেল-চকচকে বেগুন। শুক্লপক্ষের পঞ্চমীর চাঁদের মতো একফালি কুমড়ো। লাউডগাটাও উঁকি দিচ্ছে। সুব্রত অনুমান করতে পারে নিচের দিকে নিশ্চয় ঝিঙে, চিচিঙ্গে, কাঁচালঙ্কা, আরও অনেক কিছু লুকিয়ে আছে। আছে নিশ্চয়। গোটা একব্যাগ বাজার।
ব্যাগটা দেখে ওর খিদে পায়। আদিম অনন্ত খিদে। ভালো খাবারের খিদে। চায়ের দামটা দিয়ে দেয়। বেঞ্চের কোণার আড্ডাবাজ তখন ফোড়েদের নিয়ে ব্যস্ত। হাত নাড়িয়ে শরীর বেঁকিয়ে মত দিচ্ছেন, উত্তেজনায় শুনছেন না কিছুই। সুব্রত যেন এমনটাই চাইছিল। আস্তে করে পিসার হেলানো গির্জার মতো কাত করে রাখা একব্যাগ বাজার বা বাজার-ভর্তি ব্যাগটা তুলে নেয়। দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ে বাজারের মধ্যে। মিশে যায় ভিড়ে। কালকে পাঁচ-তরকারি, রবিবার লাউ-চিংড়ি, শিপ্রাটা রাঁধে ভালো। আর ঠিক তখনই ফুটপাতের ঘড়ির দোকানের সার্ভিসম্যান কাম সেলসম্যান কাম ক্যাশিয়ার কাম কমনম্যান সুব্রতর ঢেঁকুর উঠল। ভালো খাবারের ঢেঁকুর।

রোজ নামচায় খামতি ছিলো বহু
গুছিয়ে নিয়ে নেচেছি আগুন তবু
শব্দ বান তোমার ছিলো পেটে
ভাবছিলে তাই গর্দন যাক কেটে
প্রেম ছিলো না, ছিলো শুধুই ভয়
ক্ষয় হয়েছো, সময় অসীম ক্ষয়
আক্রোশে এক ভূতের গলা বেয়ে
বন্দি তুমি, বদ্ধ নিরাশ চেয়ে
খুন করেছো তোমার আদিম সত্তা
এর চেয়ে হতে আমার বাগদত্তা
শিবের লিঙ্গে জল ঢেলেছি আদিম
দুর্গা আমি, স্বামী সোহাগ স্বাধীন!

দুর্গাপূজাকে কলিযুগের অশ্বমেধ যজ্ঞ বলা হয়ে থাকে। ত্রেতাযুগে ছিল তিনভাগ পুণ্য এবং একভাগ পাপ। আর এই একভাগ পাপই ত্রেতাযুগেও অশ্বমেধ যজ্ঞকে পণ্ড করে এসেছে। ওই যজ্ঞের অশ্বগুলোকে পুজোর পর ছেড়ে দেওয়া হত এবং তারা বিভিন্ন জায়গা ঘুরে আবার যজ্ঞস্থলে এসে পৌঁছাত। কিন্তু সেই যে বলেছিলাম, ত্রেতা যুগেও একভাগ পাপ আর সেই পাপের ভাগীদার হত বিভিন্ন অসুর ও কিছু ধূর্ত রাজারা। তাদের অনৈতিক আচরণে ওই অশ্বমেধ যজ্ঞ পণ্ড হয়ে যেত। কিন্তু এটা যে কলিকাল! তিন ভাগই পাপ এবং একভাগ পুণ্য। তাই কলিযুগের অশ্বমেধে (মানে দুর্গাপুজোয়) পাপের আধিক্য বেশি থাকবে তা তো প্রায় নিশ্চিত।
প্রথম অবস্থায় যখন নিজের পাড়ার পুজোর দায়িত্বে থাকতাম তখন বুঝতাম ছোটভাবে পুজো করাই খুব কষ্টকর, আর বৃহৎ আকারে পুজোর কথা তো ভাবতেই পারতাম না। যাই হোক, পাড়ার পুজোর কাজ করতে করতে কবে যেন পুজোর শিল্পী হয়ে গেলাম। তখন থেকেই ক্লাবের চরিত্রগুলি চোখের সামনে ধরা পড়তে লাগল। হাতেগোনা কয়েকটি পুজোকে বাদ দিলে অধিকাংশই একই মানসিকতার। যেমন, যেনতেন প্রকারেণ মিষ্টি ভাষা দিয়ে ও প্রথম প্রথম ভালো ব্যবহার করে আখের গুছিয়ে নেওয়াই যেন এদের মুখ্য উদ্দেশ্য। পুজোর পরে ঘুরেও তাকায় না এরা। যতক্ষণ না পরের বছরের পুজো আসত, ততক্ষণ তারা ‘ন যযৌ ন তস্থৌ’ অবস্থায় রত থাকতেন। তাতেই ডেকরেটরের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠত, পাওনা অর্থ আদায় করতে তাদের চটির সুকতলা ক্ষয়ে যেত। এই দুরবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ডেকরেটররা একটা অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করল, যাতে আগের ডেকরেটরের ‘নো অবজেকশন’ দেখাতে না পারলে সেই পুজোতে অন্য কোনও ডেকরেটর কাজ না করে। এর মধ্যে আবার শুরু হয়ে গেছে পুজোর প্রতিযোগিতা, প্রাথমিকভাবে যাদের কাছে বাণিজ্যের থেকেও পুজোর উৎকর্ষ বৃদ্ধিই ছিল আসল লক্ষ্য। বলতে দ্বিধা নেই, এদের জন্যই পুজোর মান বাড়তে শুরু করে।
এবার ফাঁপরে পড়ল পুজোর কর্মকর্তারা। অগত্যা উপায়? পূজা-কমিটিগুলি তাদের পাড়ারই কিছু শিল্পমনস্ক ব্যক্তিকে অর্থাৎ শিল্পীকে পুজো সাজাবার দায়িত্ব অর্পণ করল নিজেরাই মালপত্র কিনে দিয়ে। সেখান থেকেই শুরু শিল্পীর আগমন, যেখানে আমদানির থেকেও ওঁদের নজর ছিল শিল্পকর্ম প্রদর্শনের দিকে। এইভাবে কিছুদিন চলার পরে তাদের নাম ডাকও বৃদ্ধি পেল।
এবার শুরু হয়ে গেল অগণিত পুজো প্রতিযোগিতার দৌড়, ছোট-বড় পুজো-সংগঠকদের মধ্যে। শুরু হল নতুন আঙ্গিকে পুজো, যার পোশাকি নাম ‘থিমপুজো’। শ্রদ্ধেয় দেবদূত ঘোষ ঠাকুরের দেওয়া নাম এটি। এই থিমপুজো হল সামগ্রিকভাবে পুজো উপস্থাপন, যাতে সমস্ত কিছুর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বজায় থাকে।
প্রথমদিকের শিল্পীদের বাড়বাড়ন্ত দেখে সবাই ভেবে ফেলল এই ক্ষেত্রটিই বুঝি অর্থ-নাম-যশের একমাত্র পথ, তাই প্রকৃত শিল্পী সহ বিভিন্ন মহল থেকে লোকেরা ‘শিল্পী’ নাম নিয়ে পুজোতে প্রবেশ করা শুরু করল। শুরুতে সবাই ভেবেছিল, বোধহয় স্বল্প বাজেটে থিমপুজো সম্ভব। আরে দাদা, যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, সেখানে সবদিক বজায় রেখে পুজো করা খুব একটা সহজ নয়! ফলে পুজোর বাজেট উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল, কিন্তু ‘সোর্স অফ ইনকাম’ তো সেই সীমিত (কিছু ক্ষেত্র বাদ দিয়ে)। তাহলে উপায়? সঙ্গে আছে তো কতিপয় অনভিজ্ঞ শিল্পী ও দিনমজুরের দল। ওরাই বলির পাঁঠা হতে শুরু করল। ‘পুরস্কার পাইয়ে দাও, অর্থ নিয়ে যাও’— এটাই হল অধিকাংশ পুজো-কমিটির অলিখিত ক্যাপশন। ফলে বাধ্য হয়েই শিল্পীরা স্বঘোষিত বিচারকদের তৈলমর্দন শুরু করল, আর যারা তা পারল না তারা দূরে সরে থাকল। ইতিমধ্যে আবার নেতারাও পুজোতে নেমে পড়েছেন জনসমক্ষে নিজেদের তুলে ধরার জন্য (অবশ্যই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য)। তাই শিল্পীদের তৈলমর্দনেও ভাটা দেখা গেল। প্রভাবের কাছে বেচারী পুরস্কারদাতারাও নিজেদের মনুষ্যত্ব হারাতে বাধ্য হল। প্রথমদিকে প্রতিযোগিতা ছিল, কে কত উচ্চমানের পুরস্কার পেতে পারে। প্রভাবের চাপের ফলে যখন সেই উচ্চমানের পুরস্কার থেকে ছোট ক্লাবগুলি বঞ্চিত হতে শুরু করল তখন থেকেই তারা পূর্বে-উপেক্ষিত পূজা বিচারক সংস্থার প্রতি ঝুঁকে পড়ল এবং সংখ্যাতত্ত্বে বিশ্বাসী হল। পুজোতে সর্বশেষ সংযোজন কর্পোরেটের প্রবেশ, যা সাধারণত নেতাদের পুজোতেই অগ্রগণ্য। তা থেকেও ছোট পুজো-কর্মকর্তারা বঞ্চিত।
একথা বলেই শেষ করছি যে, সব বউরা খারাপ হয় না। শাশুড়ির অত্যাচারে বা তার প্রতিহিংসাপরায়ণ স্বভাবের জন্য বউরা খারাপ হতে বাধ্য হয়। আবার উল্টোটাকেও ফেলে দেওয়া যায় না। ‘দিদি নম্বর ওয়ান’-এ আগত শাশুড়িরা সংখ্যায় বোধহয় খুবই কম, তাই তাদের বউয়েরাও ভালো। ঠিক তেমনই, ক্লাব কর্মকর্তারা সঠিক থাকলে শিল্পীমহলও সঠিক থাকবে। আবার শিল্পী তার কথার দাম রাখতে পারলে ক্লাব কর্মকর্তারাও নিজেদের নৈতিকতা নষ্ট করবে না। ভালো-খারাপ সর্বত্রই বিদ্যমান, তবে এ যুগে খারাপের সংখ্যাটা বেশি। শুধুই ভালো থাকার ভান দেখা যায় আর সরল মানুষ সেই ভানের পাতা ফাঁদে পড়ে যায়— তা শিল্পী হোক বা পুজো কর্মকর্তা।

এইসব সেরে গেলে
আমি বাড়ি ফিরব।
পথেঘাটে রোদ্দুরমাখা লোকজনকে
ছুঁয়ে দেব খানিক।
গাছতলা ঘেঁটে বকুলফুল কুড়োব।
কলেজস্ট্রিটের ট্রাম ধরে, লোনলি প্ল্যানেটের পাতা উল্টোতে উল্টোতে সোজা চাঁদনী গিয়ে নামব।
পুরনো নিউমার্কেটে, চটির দোকানে বসে থাকব।
বন্ধু জুটিয়ে দাশ কেবিন পৌঁছে কবিরাজি কাটলেট খাব।
মন্ত্রের মতো, মনকে শুনিয়ে যাব শুনিয়েই যাব : সেরে ওঠো,
সেরে ওঠো...
শুধু, এইসব সেরে গেলে তোমার সঙ্গে কী করব,
কাউকে বলব না

সত্যি জেনেও মানতে চায়নি মন
অথচ যেমন শিক্ষকও ভুল করে
যেমন মাটিরও ইচ্ছে অনিচ্ছেরা
পাতার হলুদে প্রতিবাদ তুলে ধরে।
গণতন্ত্রের নেতাও ফ্যাসিস্ট হয়
প্রগতিশীলের মেয়ে মরে যায় ভ্রুণে
ঈশ্বর হওয়া ডাক্তারও খুন করে
ভালো লাগে তাই মিথ্যেই যাই শুনে।
সত্যি জেনেও চোখ দুটো বুজে ফেলি
পাছে দেখে ফেলি সত্যের নগ্নতা
তুমি জানো, আমি এরকমই দুর্বল
মিথ্যে আশার সাথে করি সমঝোতা।

পাড়ায় সেবছর কোনও দুর্গা প্রতিমা এল না। ঘটের সামনে বৃদ্ধ পুরুতমশাই বিধুর মন্ত্রপাঠ করে গেলেন। পুজো প্রতিমাহীন মণ্ডপটি ফাঁকা। পুজোমণ্ডপ যে মাঠে হত তার সামনের বাড়ির একটা জানলার পাল্লা খোলা। বাকি সব জানলা দরজাগুলো বন্ধ করে রেখেছে সেই বাড়িতে। ওই বাড়ির সতেরো বছরের ছোট ছেলে কৃষ্ণ, পাড়ায় একটু সিনিয়ার বলে আমরা কেষ্টদা বলতাম। সে নকশাল করত বেশ কয়েকবছর ধরে, রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত, দু-তিনদিন পর ফিরত। পাড়ার লোকে বলত সে নাকি আন্ডারগ্রাউন্ড অ্যাকশন করে। তার ধড়মুণ্ডু আলাদা হয়ে কয়েকদিন আগে পড়েছিল বরানগর বাজারে। তারপর তার দেহটি আরও অনেক লাশের সঙ্গে ঠেলা গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে অনেকে বলাবলি করে। গঙ্গায় স্নান করতে যেতে এখন লোকে ভয় পায়। এত রক্ত কিছুদিন আগে গঙ্গা দিয়ে বয়েছে। পাড়ার বাতাসে যেন অশৌচের স্পর্শ। পাড়ার পুজোটা এবারে একেবারেই বদলে গিয়েছে।
আগস্টের বারো, তেরো, চোদ্দ, তিনদিন ধরে কাশীপুর বরানগর সংলগ্ন এলাকায় চলেছে গণহত্যা। যদিও এটাকে গণহত্যা বলি আমরা, তবে আমার কিন্তু গৃহযুদ্ধ বলতেও ইচ্ছে করে। যখন নকশাল ছেলেদের পাড়ার কংগ্রেস আর সিপিএম দাদারা খবর দিল যে জায়গায় জায়গায় বিরাট বাহিনী আসছে তাদের মারবার জন্য, তখন কিন্তু ওই বাচ্চা কিশোরবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেরা পাড়া ছেড়ে সরে পড়ল না। তারা বলল : আসছে আসুক, লড়ে মরব। তারা পাইপগান নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গলির পাশে। লড়তে গেলে মরণ হতেই পারে। যুদ্ধে তো কেউ জিতবেই আর সেই জিতবে যার জোর বেশি। কৌশলও যে যুদ্ধের জন্যে একটা গুরুতর প্রয়োজনীয় জিনিস সেটা ওই বাচ্চা ছেলেরা তখনও শিখে ওঠেনি। এদিকে কৌশল ছাড়া যুদ্ধে গেলে তুমি বেঘোরে মরবেই। হল-ও তাই। বরানগর বাজার, কাশীপুর রোড, প্রামাণিক ঘাট রোড কচি কচি ছেলেদের রক্তে ভেসে গেল। বরানগর বাজারের মাছওলার মাছ কাটার বঁটি কেড়ে নিয়েও কাটা হল তিন চারটি ছেলেকে। এছাড়া চপাতি, তরোয়াল তো ছিলই। রক্ত, বারুদ, মৃতদেহর পর মৃতদেহ।
কয়েকদিন আগে যাদের বাড়ির ছেলে মারা গেছে তাদের যেমন এবারে পুজো নেই, সেরকম যাদের বাড়ির কেউ মারা যায়নি তারাও যেন পরিজন হারানোর দুঃখে নিথর হয়ে ঘরে বসে রয়েছে।
তখনকার পাড়াগুলো তো আসলে এত বিচ্ছিন্ন ছিল না। যে যার-টা বুঝে নেওয়া ছিল না। সেই ১৯৭১ সালে পাড়াগুলো ছিল সত্যিই একেকটা পরিবারের মতো। চাপা রেষারেষি, ঈর্ষা যে কোথাও ছিল না তা নয়, তবে পরস্পরের প্রতি এখনকার মতো উদাসীনতা ছিল না। সকলে অনেক বেঁধে বেঁধে থাকত সেই সময়।
পুজোর সময় তখন বেশ ঠান্ডা পড়ে যেত। বাতাসে হিমের মৃদু স্পর্শ, রোদ্দুরে চাঁপাফুলের হলুদ রঙ। কিন্তু সেই বছর তো ঢাকের শব্দটা বিষাদসিন্ধু হয়ে গিয়েছে। আমাদের বাড়ি ছিল চূড়ান্ত নকশালবিরোধী। আমিও তখন থেকেই মনে মনে যুক্তি দিয়ে কোথাও কোনওভাবে সমর্থন করতে পারছি না নকশালপন্থীদের কাজকর্ম এবং দর্শনকে।
কিন্তু তবুও, যাকে সমর্থন করব না তাকে মেরে ফেলব এই মতেও তো আবার কখনও বিশ্বাস করতে পারিনি।
আবার এটাও ঠিক, নকশালপন্থী ছেলেপিলেরা জেনে বা না জেনে বিদেশী শক্তির একটা অনৈতিক হাতকে শক্ত করে যাচ্ছিল। আমাদের দেশের অনেক সঙ্কটকে উসকে দিয়ে, যুব সমাজকে ভ্রষ্ট করে একটা সীমাহীন নৈরাজ্য এবং অর্ধপক্ক বুলি এদেশের ছোট ছেলেমেয়েদের কাঁচা মাথায় ঢুকিয়ে দেবার একটা চেষ্টা নকশাল আন্দোলনের নেপথ্যে দাঁড়িয়ে ছিল বলে আমি চিরদিনই মনে করেছি।
একথা নির্ভুল মনে হয়েছে যে, এই সুকৌশলী নৈরাজ্যের নকশালপন্থা যে কী করে বন্ধ করা যাবে সেটা ভেবে অনেক সুস্থ বুদ্ধির মানুষও কূল পাচ্ছিলেন না।
ফলে শুরু হয়ে গিয়েছিল অস্ত্রের উত্তর অস্ত্র দিয়ে দেওয়া।
দুর্গাপুজোর মন্ডপের সামনের বাড়িতে একটা জানলার পাল্লা খোলা। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা দিবসের পরের দিন এই বাড়িতে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়।
মৃত কেষ্টদার পরিবারকে দেখে আর কিছু বলতে পারেননি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী। আশ্চর্য পরস্পরবিরোধিতায় মোড়া এই দীর্ঘকায় সুপুরুষ মানুষটি সেদিন মাথা নিচু করে কেষ্টদাদের বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়েছিলেন। কেষ্টদার মা সেদিন থেকে আর কথা বলতে পারেননি। খেতে পারেননি। চুপ করে বসেছিলেন। কোনও ভাষা নেই মুখচোখে। সেই আগেকার দিনে যখন মেয়েদের বিয়েই হত সতেরো আঠেরোয়, তখন আর সতেরো বছরের ছেলের মায়ের বয়েসই বা কত হবে। চৌত্রিশ, পঁয়ত্রিশ বছরের নিঁখুত সুন্দরী প্রতিমার মতো মুখ ছিল মাসিমার। কুচকুচে ঘন কালো একঢাল চুল। দুর্গাপ্রতিমার মতো উজ্জ্বল মুখ। শুধু চোখে কোনও জ্যোতি নেই। নিস্পলক তিনি চেয়েছিলেন। সিদ্ধার্থবাবু ওদের বাড়িতে কেষ্টদার মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে স্তিমিত স্বরে একবার বলেছিলেন ‘আমাকে কি কিছু শাস্তি দেবেন?’
কোনো উত্তর আসেনি। মুখ্যমন্ত্রী ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন খুব ধীর পদক্ষেপে।
তারপর আস্তে আস্তে একটা একটা করে দিন কাটতে লাগল। পুজো এল, প্রতিমা এল না পাড়ায়। আমাদের বাড়ির রাজনৈতিক মত যতই আলাদা হোক, আমাদের কারুর নতুন জামা হল না পুজোয়। আমাদেরও মন সায় দিল না নতুন জামা পরে ওই খাঁ খাঁ করা বাড়িটার সামনের মণ্ডপে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে। মণ্ডপটাকে তো ঠিকমতো মণ্ডপই মনে হচ্ছে না এবারে। বারবার চোখ চলে যাচ্ছে সামনের বাড়ির দিকে।
দশমীর দিন দর্পণে বিসর্জনের পরে পাড়ার মহিলারা গিয়ে দাঁড়ালেন কেষ্টদাদের বাড়ির সামনে। পুরুষরাও দাঁড়িয়ে রইলেন একটু দূরে। মাসিমা কয়েকমাস অনাহারের পর আজ ভোরে চলে গিয়েছেন নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে। তাঁর মৃতদেহ বাড়ির দালানে নামল। পাড়ার এয়োস্ত্রী মহিলারা সিঁদুর দিতে লাগলেন একে একে। পুজোয় পাড়ায় এবার কিছুই হয়নি। এখন যেন বিজয়া দশমীর সিঁদুরখেলাটুকু হঠাৎ চমকে দিয়ে দেখা দিল। এই সমাপতনের মধ্যে অনেকের মনে পড়ল কেষ্টদার মায়ের পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল মহামায়া।
শুভ বিজয়া।
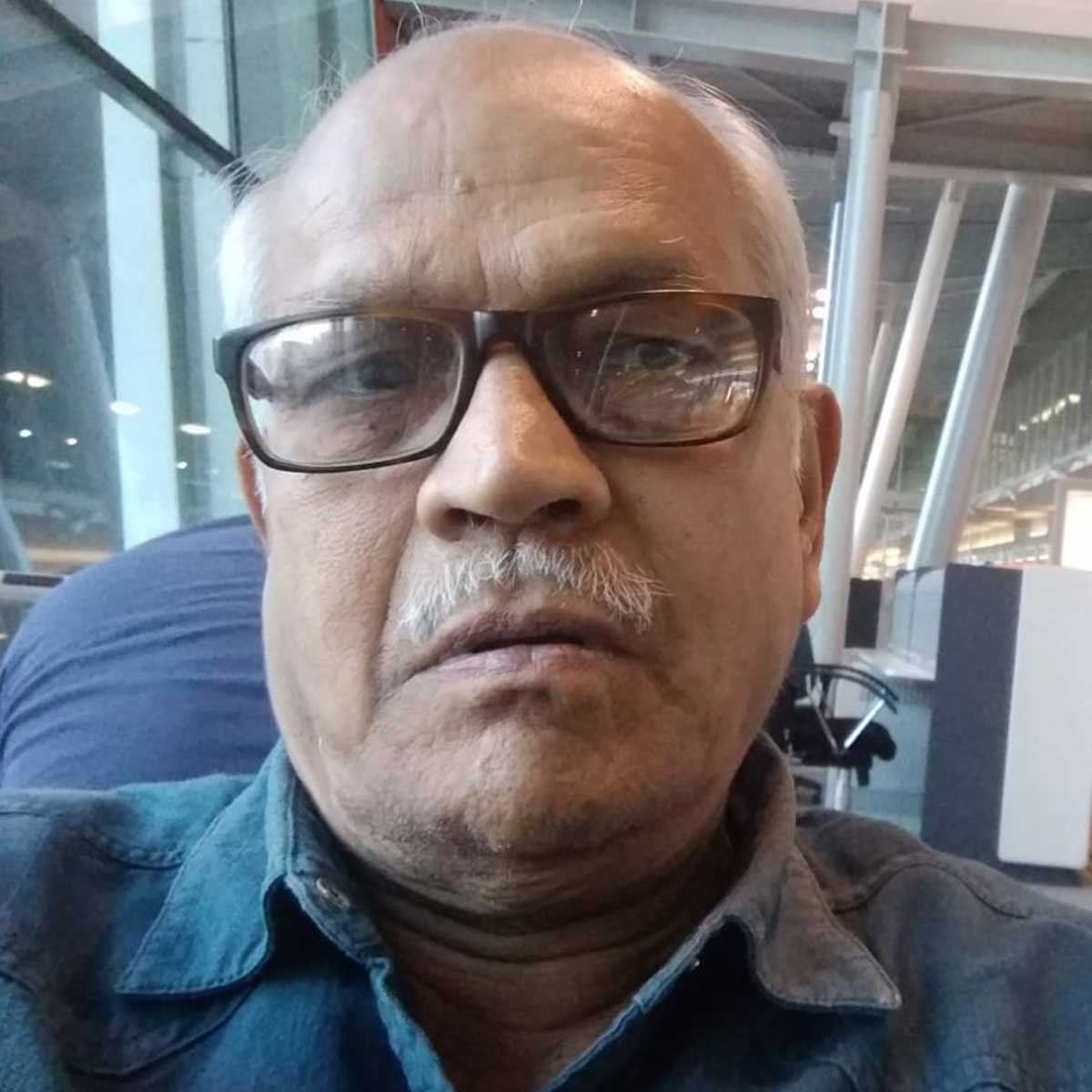
এখনকার মতো বিনোদনের নানা রঙিন পসরা তখন ছিল না। ছিল না পুজো নিয়ে কোনও প্রতিযোগিতা! ‘থিম’ পুজোর ব্যাপারটা তখনও চিন্তার বাইরে! এমনকী আধা-শহরেও তখন পুজো মানে ‘পুজো’ই! পুজোর চারটে দিন নতুন জামা-প্যান্ট বা পাজামা-পাঞ্জাবি চড়িয়ে মণ্ডপে ঢাকির বাজনার তালে শরীর দোলানো কিংবা সুযোগ পেলে কাঁসর আর ঘন্টা নিয়ে আরতির সময় সন্ধ্যাবেলা একটু বাজানো-টাজানো। আর তারই ফাঁকে ভিনপাড়ার কিশোরী অতসী বা প্রতিমার সঙ্গে লুকিয়েচুরিয়ে দৃষ্টি বিনিময়!
দশমী কেটে যাওয়ার পরই বড় আকর্ষণ ছিল ‘বিজয়া সম্মিলনী’। মজার কথা, এই বিজয়া সম্মিলনী তখন চলত কালীপুজো পর্যন্ত। একরাত্তির নয়, অন্তত তিন রাত্তির তো বটেই। খুব ছোটবেলায় পুজোর চারদিন হোল-নাইট যাত্রা হতো আমাদের বাজারে। কলকাতার নট্ট অপেরা, মঞ্জরী অপেরার মতো ডাকসাইটে দল রাতভোর ‘বিল্বমঙ্গল’ থেকে ‘সাবিত্রী সত্যবান’ পালা দেখাত। কোনওদিন মাঝরাতের পর পালা শেষ হলে ভোর পর্যন্ত আসরের চটে শুয়েই ভোর কাবার করতাম। তবে সবচাইতে উত্তেজনা ছিল সম্মিলনীর শেষ দিন। সেদিন ‘বিচিত্রানুষ্ঠান’ হবে! কলকাতা থেকে পিন্টু দাশগুপ্ত আসবেন হাসির গান নিয়ে। আসবেন ‘জনপ্রিয়’ গায়ক তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর হাস্যকৌতুক পরিবেশনায় হাজির থাকবেন শীতল মুখার্জি, নবদ্বীপ হালদার আর অজিত চট্টোপাধ্যায়। এই ক’জনকে পেয়েই খুশিতে ডগমগ আমরা।
ক’বছর বাদে স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে আধা-শহরে এসে দেখলাম সেই বিচিত্রানুষ্ঠানের অন্য চেহারা! রাত আটটায় শুরু হয়ে প্রায় ভোর পর্যন্ত চলেছে শিল্পীদের আগমন-নির্গমন। কে নেই সেখানে! হেমন্ত-শ্যামল-মানবেন্দ্র-সতীনাথ-উৎপলা-সুবীর সেন-নির্মলা-হৈমন্তীদের সঙ্গে স্টপগ্যাপ হিসেবে অনেক সময়েই ঢুকে পড়ত পাড়ার উঠতি কোনও কোনও হেমন্ত বা সন্ধ্যা-লতাকণ্ঠী। পুজোর কর্তাব্যক্তিদের উদারতায় আর কী!
সময় তো পিছিয়ে থাকে না, এগিয়েই যায়। আর সেই অগ্রগতির সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিয়ে পিছিয়ে যেতে থাকে পুজোর আসল উদ্দেশ্য— আন্তরিকতা ও ভক্তি! বাজারের নিয়ম রেখে ‘পুজো’কে ব্যবসায় রূপান্তরিত করে তোলে মানুষের হুজুগ এবং কর্পোরেট জগৎ। শুরু হয় থিম পুজো, পুজোর প্রতিযোগিতা! ভক্তি আর আন্তরিকতাকে আটচালার আড়ালে সরিয়ে সামনে এসে পড়ে চোখ-ধাঁধাঁনো জৌলুস আর ব্যবসায়িক কূটনীতি! পুজোর চাইতে বড় হয়ে ওঠে বাহ্যিক আড়ম্বর। তখন তো স্পষ্ট করে বলাও হয় কয়েকশো কোটি টাকার ‘ব্যবসা’ জড়িত বাঙালির সেরা উৎসব এই দুর্গাপুজোর জন্য! যে কারণে এখন অতিমারী-মহামারীর মধ্যেও সরকারি তোষাখানা খুলে দেওয়া হল!
এখন আর ‘বিজয়া সম্মিলনী’ হতে দেখি না বড় একটা, অন্তত কলকাতা শহরে। এখন অনুষ্ঠান বলতে— যাকে এক কথায় বলা যায় ‘মাচা’— সেটাই এখন লোকবিনোদন। শুধু গান নয়, ছোট-বড় পর্দার নায়ক-নায়িকাদের এনে সিনেমার জনপ্রিয় গান বাজিয়ে নাচের অনুষ্ঠানই এখন বড় অনুষ্ঠান। পড়শিরাজ্য বিহার থেকে ‘ঝুমকা গিরা’ নাচনিদেরও ডিম্যান্ড কম নয়। ক্লাবের রেস্ত থাকলে ডিজে মঞ্চে উঠিয়ে উৎসাহী উদ্যোক্তারাও এখন নায়ক-নায়িকার নাচের সঙ্গে শরীর দোলানোর ব্যর্থ চেষ্টাতেই আনন্দ পান। ‘ফুর্তির বন্যা’ যাকে বলা যায় আর কী! এই ‘মাচা’ ফাংশনের জন্যই টলিউডের মাঝারি ও ছোট মাপের শিল্পীদের এত রমরমা। পুজোর পর থেকেই প্রায় পুরো শীতকালটা, প্রায় চার-পাঁচ মাস মাচার খাঁচায় বন্দি থাকেন এঁরা। বছরকার রান্নাঘরের বিলাসী খরচ তো এখান থেকেই জোগাড় হয়। ছবি করে আর ক’পয়সা! আর ছিল গাঁ-গঞ্জের যাত্রা। এখনও আছে। বাংলার লোকসংস্কৃতির তলানিটুকু তো আটকে আছে এখনও যাত্রাপালাতেই।
তবে এবারের অবস্থা বেমালুম আলাদা। করোনাভাইরাসের কামড়ে সব শিল্পই এক ঘোরতর সংকটে। শিল্পের সঙ্গে জড়িত সব মানুষরাও। কুমোরটুলির প্রতিমাশিল্পী থেকে ঢাকি, অন্যদিকে মাচাকরিয়ের দল তো বটেই এবং আনুষঙ্গিক সব শ্রেণীর মানুষই এই মুহূর্তে শারীরিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে ব্যস্ত। ব্যস্ত শুধু নয়, বিধ্বস্তও বলা যায়।
এমন মহামারী আমরা আর ক’জন দেখেছি! শারদীয়া পুজোর যে এমন লণ্ডভণ্ড চেহারা হবে তা ছিল কল্পনার বাইরে। পুজোর বিনোদন এবছর যে কেমন চেহারা নেবে এখনও বোঝা যাচ্ছে না। সরকারি অনুদানে হয়তো পুজোগুলো হবে, কিন্তু দর্শনার্থীদের হাজিরা নিয়ে সংশয় থাকছেই। এই তো কেরালার ‘ওনাম’ উৎসবের পরই সেই রাজ্যে করোনা সংক্রমণ বিপজ্জনক চেহারা নিয়েছে খবর পাচ্ছি। এত দুঃখের মধ্যেও এক চিলতে আনন্দের খবর হল— সিনেমাহলগুলো অর্ধেক আসন নিয়ে খুলছে পুজোর আগেই। দর্শকসংখ্যা কেমন হবে তা নিয়ে বিভ্রান্তি-সন্দেহ রয়েইছে। কিন্তু এই অতিমারীর সময়েও ‘পুজোর ছবি’কে আটকানো গেল না। এবার পুজোতেই মুক্তি পাবে সম্ভবত অল্প পরিচিত পরিচালকদের ছবি। সৃজিত-কৌশিক-অরিন্দম-রাজ চক্রবর্তীরা এমন অস্বস্তিজনক পরিস্থিতিতে নিজেদের ছবিকে সরিয়ে রাখছেন। হয়তো কালীপুজো বা আরও পরে বর্ষশেষ বা নতুন বর্ষে আসবে তাঁদের ছবি। এই বছরটা তাই সৌকর্য ঘোষাল (রক্তরহস্য), অর্জুন দত্ত (গুলদস্তা), দেবালয় ভট্টাচার্য (ড্রাকুলা স্যার), অংশুমান প্রত্যুষ (এসওএস কলকাতা)-দের জন্য বরাদ্দ থাকছে। ব্যতিক্রম শুধু অঞ্জন দত্তর ছবি ‘সাহেবের কাটলেট’। শহুরে শিক্ষিত সংখ্যালঘু দর্শকের কাছে তিনি ও তাঁর ছবি সমাদৃত। পুজোর শহরে তাই অঞ্জন সাহসে ভর করেই ছবির মুক্তিতে রাজি।
পুজো কোনওরকম বাড়তি বিপদ না আনলে সেই বিজয়া সম্মিলনী বা বিচিত্রানুষ্ঠান কি এবার ফিরবে? প্রশ্নচিহ্ন থাকছেই। মাচা অন্তত এবছর আর তৈরি হবে না— সেটা সব্বাই বুঝে গেছেন। মাচার শিল্পীরাও তাই ‘বিকল্প’ খুঁজছেন। কেউ ছোটপর্দার ধারাবাহিকে বা কোনও মিউজিক্যাল শো বা চ্যাট শো-এ নিজেদের ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছেন। রান্নাঘরের গ্যাসওভেনটা তো জ্বালাতেই হবে রোজ। সেই জ্বালানির খরচ তো চাই! অগত্যা। এবছর আর শহরে তো নয়ই, শহরতলির পাড়ায় পাড়ায় জলসা হবে কিনা শতভাগ সন্দেহ! পয়সা না থাকায় টিকিট কাটতে না পেরে প্যান্ডেলের বাইরে দাঁড়িয়ে কুমার শানু, অভিজিৎ, অরিজিৎ সিং বা মনোময়-শ্রীকান্ত-লোপামুদ্রা বা জোজোর গান শোনা এখন স্মৃতির পাতায়। এবারের দুর্যোগ নতুন এক ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছে যেন! রেকর্ড-ক্যাসেট পেরিয়ে এখন যেমন ইউটিউবে বা নিজস্ব ফেসবুকে গান আপলোড করে শ্রোতাদের কাছে পৌঁছচ্ছেন শিল্পীরা, আগামীতে সম্ভবত সেটাই হতে যাচ্ছে ‘নিউ নর্ম্যাল’ থেকে ‘নর্ম্যাল’। ‘পয়সা ডালো গান শুনো’— এমন ধারাটাই হতে যাচ্ছে করোনাভাইরাস-পরবর্তী বিনোদন। হাতের মুঠোতেই মিলবেন সবাই। ভারততীর্থের মহাসাগর হবে হাতের মুঠোর অ্যান্ড্রয়েড ফোন। চিৎকারে তাই বলাই যায়, দুর্গা মাঈ কি নয়, করোনা মাঈ কি জিন্দাবাদ।

বই-খাতা সব গুছিয়ে রাখো
বাজছে কাঁসি কাঁই-না-নানা,
তোমাকে কেউ বলছে যেন,
‘এই ছেলেটা, বাইরে যা না’।
কোথায় যাবে? খুশি তোমার
বেড়িয়ে এসো ভোমরাগুড়ি,
ঢাকের বাদ্যি ডাকছে তোমায়
ঘিন্চিকুড়ি, ঘিন্চিকুড়ি।
ওই দ্যাখো না আস্তে-আস্তে
মিলিয়ে যাচ্ছে মেঘের কালো,
বারান্দাতে দাঁড়াও, দেখবে
শিউলিফুলে বাগান আলো।
দেখবে ছবির মতো আকাশ
মাঠে সবুজ ছড়িয়ে আছে,
নিমন্ত্রণের রঙিন চিঠি
উড়ছে তোমার হাতের কাছে।
পুজোর আগে
উড়ছে পালক, ফুরফুরে মেঘ, কাগজকুচি, তুলো
তুলতুলে রোদ ভরিয়ে দিল বিষণ্ণ মুখগুলো।
একখানা নীল পাঁচখানা নীল সাতখানা নীল এসে,
সাতসকালে হুতুমথুমো আকাশটাতে মেশে।
সেই আকাশের ঝিলিক দেখে ছাতিম গাছের পাতা,
ভুবনডাঙায় পাঠিয়ে দিল পদ্যলেখার পাতা।
খাতায় খাতায় তাকুড় নাকুড়, লতায় পাতায় মিল,
মিলের টানে মেলা বসায় ঘরভোলা গাঙচিল।
সন্ধেবেলায় ফটফটিয়ে জ্যোৎস্না এসে নামে,
ডিহিপসলা, ঝুমঝুমি আর পাকুড়দানা গ্রামে।
রাজনগরের মাঠ উজিয়ে চলছে চাঁদের গাড়ি,
আপনমনে ডিগবাজি খায় নফর বসুর বাড়ি।
বাড়ির পাশে ভিড় করেছে শিউলি টগরেরা,
ঝিম্ধরানো সুবাস দিয়ে বাগানগুলো ঘেরা।
এমন সময় কাঁসাই নদী কোথায় যেন যায়,
গানের সুরে আটকে গেল গাড়িবারান্দায়।
গিজতা গিজাং গিজতা গিজাং পড়ল ঢাকে কাঠি,
পুজোর আগেই পৌঁছে গেলাম বল্লুক-সেনহাটি।
পুজোর চিঠি
একটা চিঠিতে ফুলের গন্ধ, রঙে ভরপুর পাখি,
একটা চিঠির খোলা জান্লায় রোদ্দুর মাখামাখি।
একটা চিঠির নীলচে কাগজে শিউলি ও কাশফুল,
খেয়ালখুশির ছোট্ট নদীটি কুলুকুল, কুলুকুল।
একটা চিঠিতে গিজগিজে ভিড়, মাথাউঁচু ঘরবাড়ি,
একটা চিঠিতে কু-ঝিকঝিক রেলগাড়ি, রেলগাড়ি।
একটা চিঠিতে ভোরের আকাশ, ফুরফুর করে হাওয়া,
একটা চিঠিতে হাওয়াই জাহাজ, দূরান্তে ভেসে যাওয়া।
একটা চিঠিতে ঢাকের বাদ্যি, একটা চিঠিতে বাঁশি,
একটা চিঠিতে কবিতা ও গান বেজে ওঠে পাশাপাশি।
চিঠিতে চিঠিতে কত ঝিকিমিকি, তারা-ফুটে-ওঠা আলো,
একটা চিঠির ময়লা কাগজ মাথা নীচু, মুখ কালো।
একটা চিঠির ঠিকানায় ভুল, ছেঁড়াখোঁড়া কিছু লেখা,
সূর্য ডুবেছে… মাঠের আড়ালে আঁকাবাঁকা পথরেখা।
পুকুরের জলে মাছ ঘাই মারে, বাঁশপাতা খসে পড়ে,
এবড়োখেবড়ো রাস্তায় আর চালফুটো কুঁড়েঘরে।
টিমটিম করে লম্ফের আলো, থমথম করে রাত,
ভাঙা এনামেল থালায় সাজানো স্বপ্নের ডালভাত।
ছোটো হয়ে আসে আকাশের চাঁদ, উল্কাও পড়ে খসে,
বোন ঘুমে কাদা, চুপচাপ বাবা দাওয়ায় রয়েছে বসে।
চিঠির কাগজ ভিজে জবজবে, মায়ের দু’চোখ ভারী:
“পূজায় এবার আমার জন্য কিনিও না আর শাড়ি।
বাবার জন্য ফতুয়া কিনিও, বোনের জন্য জামা,
ঝুমাকে ফিতা ও চুড়ি দিয়াছেন তোমার বিনোদমামা।
এবার এ-গ্রামে পূজা হইবে না, গ্রাম নাই গ্রামে আর,
রাক্ষুসি নদী সব খাইয়াছে, বাড়িঘর ছারখার।
পূজার বদলে নদীর বাঁধ ও রাস্তা সারাই হবে,
ষষ্ঠীর আর কয়দিন বাকি… বাড়ি পঁহুছিবে কবে?
তোমার দিদিমা হয়তো আসিবে মহাষ্টমীর দিনে,
পারিলে একটা জল খাইবার গেলাস আনিও কিনে।
পত্রে তোমার কুশল লিখিও, মনে কিছু করিও না,
আমরা মরিয়া প্রাণে বেঁচে আছি, আশীর্বাদিকা মা।”
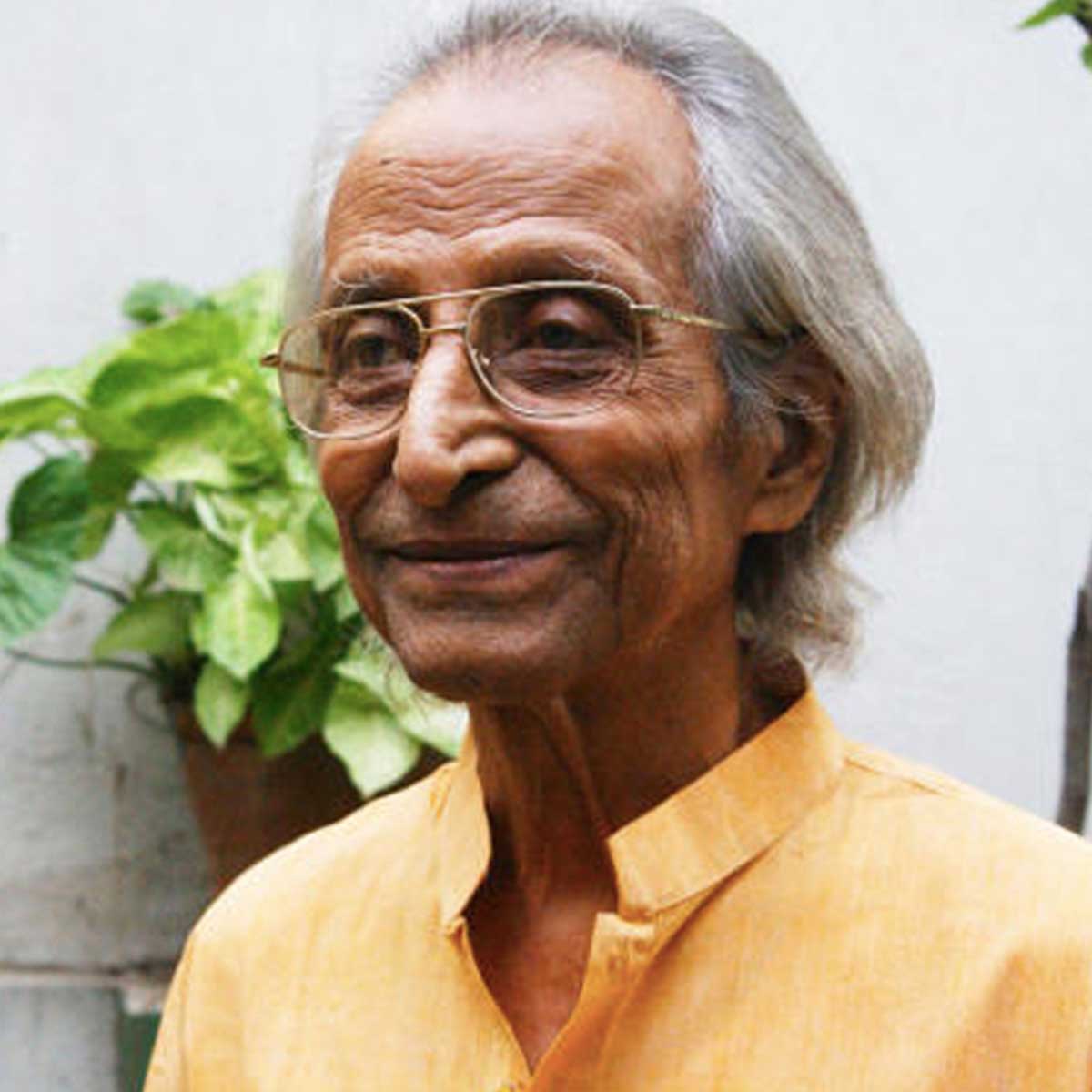
এক জার্মান দার্শনিক হিটলারের আমলে আমাদের সচেতন করেছিলেন এই বলে— তোমরা সবাই ছোট মানুষ (লিটল ম্যান) তোমাদের কোনও প্রশ্নের অধিকার আছে কি? বৃহৎ রাষ্ট্রযন্ত্রে তোমাদের অস্তিত্বটা কোথায়! তা কি অনুধাবন করতে পেরেছ? নাটবল্টুদের কোনও প্রশ্ন থাকা উচিত নয়। নিজের চেষ্টায় কিছু কাল বেঁচে থাক, তারপর অসীম অনন্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাও। তবু প্রশ্ন আসে, উত্তর খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টায় কিছুটা সময় কাটে। তারপরে সেই বিখ্যাত এক কবি ও নাট্যকার শেক্সপিয়রের কথায়— ‘It is a tale told by an idiot, full of sound and fury signifying nothing.’ প্রবীণ হয়েছি, অতীতের অনেকটাই দেখার সুযোগ হয়েছে। মস্তিষ্কের একটি কুঠুরীতে সে সব সঞ্চিত আছে। প্রশ্নও আছে অনেক। প্রথম প্রশ্ন— ভারতবর্ষের মতো ঐতিহ্যপূর্ণ, ইতিহাস সমৃদ্ধ এই বিশাল দেশটিকে কোন অবাঞ্ছিত শক্তি টুকরো টুকরো করে দিয়ে গেল? আর সেটা মেনে নেওয়া হল কেন? আবার বলা হল, ভারতবর্ষ এই পৃথিবীর একটি বিরাট ‘গণতন্ত্র’। তন্ত্র শব্দটি তো বোঝা গেল, কিন্তু গণ বা জনগণেশের এই তন্ত্রে কতটা অধিকার বা সচেতন ভূমিকা স্বীকৃত?
আর এক বিখ্যাত কবি কোলরিজ জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে দাবা খেলেছিলেন। সে যেন শকুনির পাশা খেলা। ১৯৪০ সালে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মৌলনা আবুল কালাম আজাদ একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন, ‘It was India’s historic destiny that many human races and cultures and religions should flow to her, finding a home in her hospitable soil, and that many a caravan should find rest here…’ তিনি এগারোশো বছরের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, আমাদের ভাষা, কবিতা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আমাদের ফ্যাশান, সাজপোশাক, আমাদের চালচলন এবং প্রথা— সবই কিন্তু বহন করছে ঐক্যের সুর। আমরা একসঙ্গে বেঁচে আছি এবং বেঁচে থাকার ধরন-ধারন, আমাদের জাতীয়তা বোধ— সবকিছুকেই একটা ছাঁচে ঢালাই করে ফেলেছি। কোনও ভাবেই এই ঐক্যকে ভাঙা সম্ভব নয়। এ যেন সেই কবির কথা— ‘শক-হুন-দল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন।’
একই সময়ে (১৯৪০ সাল) মুসলিম লিগের প্রেসিডেন্ট জিন্নাহ বললেন, ‘It is a dream that the Hindus and Muslims can ever evolve a common nationality; and this misconception of one Indian nation has gone far beyond the limits and is the cause of more of our troubles and will lead India to destruction if we fail to revise our notions in time. The Hindus and Muslims belong to two different religious philosophies, social customs, and literature. They neither intermarry nor interdine together, and indeed they belong to two different civilisations which are based mainly on conflicting ideas and conceptions. Their aspects on life, and of life, are different.’
তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রথম থেকেই দুই শিবিরের পরস্পর বিরোধী দু’টি ধারণার সংঘাত। জিন্নাহ সাহেব তাঁর সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ আলাদা একটি বিভাজনে রাখার স্বপক্ষে যুক্তি খাড়া করছেন। হিন্দুর জীবন ও সংস্কৃতি এবং মুসলিমদের জীবন ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। সু’টি জাতির দুই মেরুতে অবস্থান। ‘জাগে নব ভারতের জনতা / এক জাতি এক প্রাণ একতা’ এটি সঙ্গীতেই থাক। বাস্তব জীবনে এই একতা আসেনি, আসবেও না।
এই বিভাজনের অস্ত্রটি বিদেশী শাসকরা খুব সুচারুভাবে ব্যবহার করে প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। তারই ফল চতুর্দিকে ফলছে। প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। প্রকৃত সমস্যাকে আড়াল করে দাঁড়াচ্ছে। ‘রোটি, কাপড়া অউর মকান’— এই যে চাহিদা যা ধর্ম, জাতি, ভাষা, বর্ণ— কোনও কিছুই মানে না। সবার উর্দ্ধে জনজীবনের বিকাশের যে ইস্যুটি বারেবারে হারিয়ে যায়, তা হারায় এই বিভাজনের ঘোলা জলে।
কারও মাথাতেই আসে না আসল সমস্যাটা কী? তৈরি করা সমস্যার মেঘের আড়ালে দাঁড়িয়ে কয়েকটি কথার বাণ ছুঁড়ে যাঁরা হিরো হতে চান তাঁদের বরাতে সব শেষে জোটে একটি সুন্দর ‘জিরো’। এই খেলাটিকে রপ্ত করার নামই রাজনীতি। কল্যাণ শব্দটির বিস্তার পরিধি কতটা? আদৌ কি আমরা কল্যাণ চাই? উত্তেজনাশূন্য শান্ত জীবন চাই, সুখী পরিবার চাই, সুন্দর নিরাপদ একটা দেশ চাই! সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, আমাদের ধর্মের কোনও সঠিক রূপ আমরা তৈরি করতে পেরেছি কি?
আজকের বাঁচাটা কালকের বেঁচে থাকাকে উদ্বুদ্ধ করবে কি? সাধারণ মানুষের অতি সাধারণ কিছু প্রশ্নের উত্তর কেউ কি দেবেন? কিছু দান, কিছু তোষণ, কিছু পিঠ চাপড়ানো, কিছু আলিঙ্গন ইত্যাদি যেসব দৃশ্য সংবাদমাধ্যমে ভেসে ওঠে তার পেছনে কোনও জনদরদী স্থায়ী পরিকল্পনা আছে কি? গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেই কি নেতা হওয়া যায়? চড় মেরে চুমু খেয়ে কে কবে কার মন জয় করতে পেরেছে! একটি গানের একটি লাইন চিরসমাদৃত হবে— কয়েকটি শব্দ— প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্ত্র। গৌতম বুদ্ধ থেকে স্বামী বিবেকানন্দ, খ্রিষ্ট হতে শ্রীচৈতন্য, কোরান থেকে বাইবেল, বেদান্ত থেকে বৈষ্ণব— একটি কথাই তো পতাকার মতো তুলে রেখেছেন— সবার ওপরে মানুষ সত্য। সেবাই তো ধর্ম।
সবশেষে একটি প্রশ্ন— তাহলে?
** এই ওয়েবসাইট-টিকে সমৃদ্ধ করার জন্য আপনার মূল্যবান মতামত খুব জরুরী। আপনার মতামত আমাদের ই-মেল করুন।
Your suggestion is important to us to enrich this website. Please write to us in the below e-mail.
digitaldurga2020@gmail.com